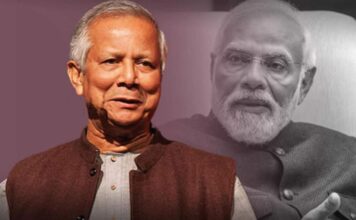ভারতের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম (Indian Startup Ecosystem) গত এক দশকে অভূতপূর্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং এটি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ হাব হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০২৪ সালে ১.২৮ লক্ষেরও বেশি স্টার্টআপ এবং ১১৮টি ইউনিকর্ন (১ বিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যায়নের স্টার্টআপ) নিয়ে ভারত ইতিমধ্যেই উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম ২.৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২.৪ লক্ষ স্টার্টআপে পৌঁছবে এবং ইউনিকর্নের সংখ্যা ২৫০-২৮০-এ উন্নীত হবে। এই প্রতিবেদনে আমরা ২০৩০ সালে ভারতের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের ভবিষ্যৎ, এর চালিকাশক্তি, চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করব।
২০৩০ সালে Indian Startup Ecosystem চিত্র
২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম বিশ্বব্যাপী উদ্ভাবনের একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে, যা প্রযুক্তি, টেকসই উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোক্তার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে। এই বৃদ্ধির পিছনে মূল চালিকাশক্তি হল:
ডিজিটাল রূপান্তর: ২০২৪ সালে ভারতের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯০০ মিলিয়ন ছাড়িয়েছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এটি ১.২ বিলিয়নে পৌঁছবে। স্মার্টফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যাও ১.১ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে। এই ডিজিটাল বিস্তার ফিনটেক, ই-কমার্স, এডটেক এবং হেলথটেকের মতো খাতে স্টার্টআপগুলির জন্য বিশাল বাজার তৈরি করবে।
তরুণ ও প্রযুক্তি-দক্ষ জনশক্তি: ভারতের ৬৬% জনসংখ্যা ৩৫ বছরের নিচে, এবং এই তরুণ জনশক্তি STEM (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত) শিক্ষায় দক্ষ। এই জনশক্তি ২০৩০ সালের মধ্যে ৫৩৫ মিলিয়ন শ্রমশক্তি হিসেবে যোগ দেবে, যা স্টার্টআপগুলির জন্য উদ্ভাবনী সমাধান এবং প্রতিভার উৎস হবে।
সরকারি উদ্যোগ: স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া এবং প্রোডাকশন-লিঙ্কড ইনসেনটিভ (PLI) স্কিমের মতো সরকারি উদ্যোগ স্টার্টআপগুলির জন্য আর্থিক, নিয়ন্ত্রক এবং অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদান করছে। ২০২৪-২৫ সালের বাজেটে সেমিকন্ডাক্টর এবং অটোমোবাইল খাতের জন্য PLI তহবিল বৃদ্ধি (যথাক্রমে ৩৬০% এবং ৬২৩%) এই প্রচেষ্টার প্রমাণ।
বিনিয়োগের প্রবাহ: ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ভারতীয় স্টার্টআপগুলি ১৫১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার তহবিল সংগ্রহ করেছে, এবং ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ এটি ১৭০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। ফিনটেক, ক্লিনটেক, এআই এবং ডিপটেকের মতো খাতে বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বাড়ছে।
প্রধান খাত এবং তাদের ভবিষ্যৎ
২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে কয়েকটি খাত প্রাধান্য পাবে:
ফিনটেক: ভারতের ফিনটেক খাত ২০৩০ সালের মধ্যে ২.১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজার সুযোগ তৈরি করবে। ইউনিফাইড পেমেন্টস ইন্টারফেস (UPI) এর মাধ্যমে প্রতি মাসে ১০ বিলিয়নের বেশি লেনদেন এবং ২৫টি ফিনটেক ইউনিকর্ন এই খাতের শক্তি প্রদর্শন করে। মোবিকুইকের মতো স্টার্টআপগুলি আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং ডিজিটাল পেমেন্টে বিপ্লব ঘটাচ্ছে।
ই-কমার্স: ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের ই-কমার্স বাজার ৪০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছবে, যা ১৯% বার্ষিক বৃদ্ধির হারে (CAGR) বাড়বে। ৫০০ মিলিয়নের বেশি ক্রেতা এই খাতকে চালিত করবে। ইউনিকমার্সের মতো কোম্পানিগুলি ই-কমার্স অবকাঠামোকে শক্তিশালী করছে।
এডটেক: শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরের ফলে এডটেক বাজার ২০৩০ সালের মধ্যে ২৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে। গ্রামীণ এলাকায় ইন্টারনেটের প্রবেশ এবং আপস্কিলিংয়ের চাহিদা এই খাতের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করছে।
হেলথটেক: হেলথটেক খাত ২০৩০ সালের মধ্যে ৬৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে, যা ২৭% বার্ষিক বৃদ্ধির হারে বাড়বে। ইন্টারনেট অফ মেডিকেল থিংস (IoMT) এবং পরিধানযোগ্য প্রযুক্তির গ্রহণ এই খাতে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে।
ক্লিনটেক এবং ডিপটেক: টেকসই উন্নয়ন এবং এআই-চালিত উদ্ভাবনের উপর ক্রমবর্ধমান জোর দেওয়া হচ্ছে। ক্লিনটেক এবং ডিপটেক স্টার্টআপগুলি ২০২৪ সালে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ আকর্ষণ করেছে, এবং এই প্রবণতা ২০৩০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।
চ্যালেঞ্জ এবং সমাধান
ভারতের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের সামনে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে:
নিয়ন্ত্রক জটিলতা: যদিও সরকার অনেক বাধা দূর করেছে, তবুও শ্রম আইন, কর ব্যবস্থা এবং সম্মতি সংক্রান্ত সমস্যাগুলি স্টার্টআপগুলির জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রক্রিয়াগুলিকে আরও সরল করা প্রয়োজন।
গ্রামীণ বাজারে প্রবেশ: অবকাঠামোগত ঘাটতির কারণে গ্রামীণ বাজারে প্রবেশ করা চ্যালেঞ্জিং। সরকার, স্টার্টআপ এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সহযোগিতা এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।
তহবিলের অস্থিরতা: ২০২২ সাল থেকে ‘ফান্ডিং উইন্টার’ এর কারণে তহবিল কমেছে, বিশেষ করে সিড এবং প্রাথমিক পর্যায়ে। তবে, ২০২৪ সালের প্রথমার্ধে তহবিল ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরে আসার ইঙ্গিত দেয়।
কর্পোরেট গভর্ন্যান্স: অস্বাস্থ্যকর কর্পোরেট গভর্ন্যান্স এবং দ্রুত মূল্যায়নের দৌড় স্টার্টআপগুলির টেকসই বৃদ্ধির পথে বাধা।
এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার ইতিমধ্যে পদক্ষেপ নিচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া সিড ফান্ড স্কিম এবং অটল ইনোভেশন মিশনের মতো উদ্যোগ নতুন স্টার্টআপগুলিকে আর্থিক এবং পরামর্শমূলক সহায়তা প্রদান করছে।
কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক প্রভাব
২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের স্টার্টআপগুলি ৫০ মিলিয়ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, যার মধ্যে ৪-৫ মিলিয়ন হবে সরাসরি হোয়াইট-কলার চাকরি, ৯-১০ মিলিয়ন গিগ ইকোনমিতে এবং ৩৫-৪০ মিলিয়ন পরোক্ষ চাকরি। এই কর্মসংস্থান অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে, বিশেষ করে অটোমোবাইল, ভোগ্যপণ্য এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি খাতে।
তবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টির গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। ২০২৩ সালের একটি RBI জরিপে দেখা গেছে, ৬০% স্টার্টআপে ১০ জনের কম কর্মচারী রয়েছে, এবং মাত্র ৮.৪২% প্রাথমিক পর্যায়ের উদ্যোক্তারা পাঁচ বছরে পাঁচটির বেশি চাকরি সৃষ্টির আশা করছেন। এটি ইঙ্গিত দেয় যে ভারতের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে আরও পরিপক্ক হতে হবে।
মহিলা উদ্যোক্তাদের উত্থান
মহিলা-নেতৃত্বাধীন স্টার্টআপগুলি ভারতের ইকোসিস্টেমে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। ২০২৪ সালে মহিলা-নেতৃত্বাধীন স্টার্টআপগুলির তহবিল ৯৩% বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং বর্তমানে ১৭,০০০-এর বেশি মহিলা-নেতৃত্বাধীন স্টার্টআপ রয়েছে। ২০টি ইউনিকর্ন মহিলা উদ্যোক্তাদের দ্বারা পরিচালিত, যা লিঙ্গ বৈচিত্র্যের উন্নতির প্রমাণ।
আঞ্চলিক বিস্তার
যদিও বেঙ্গালুরু, দিল্লি এবং মুম্বই ঐতিহ্যগত স্টার্টআপ হাব, তবে পুনে, চেন্নাই এবং হায়দ্রাবাদের মতো টিয়ার-২ শহরগুলি দ্রুত উঠে আসছে। ২০২৩ সালে ৪৫% নতুন স্টার্টআপ টিয়ার-২ এবং টিয়ার-৩ শহর থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যা স্থানীয় সমস্যা সমাধান, উন্নত অবকাঠামো এবং ডিজিটাল-ফার্স্ট ব্যবসায়িক মডেলের উপর নির্ভর করে।
২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম একটি বিশ্বব্যাপী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে, যা প্রযুক্তি, টেকসই উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোক্তার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে। ফিনটেক, ই-কমার্স, এডটেক, হেলথটেক এবং ক্লিনটেকের মতো খাতগুলি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নেতৃত্ব দেবে। তবে, নিয়ন্ত্রক জটিলতা, তহবিলের অস্থিরতা এবং গ্রামীণ বাজারে প্রবেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। সরকার, বিনিয়োগকারী এবং উদ্যোক্তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভারত ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের শীর্ষ স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, যা দেশের অর্থনীতি এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।